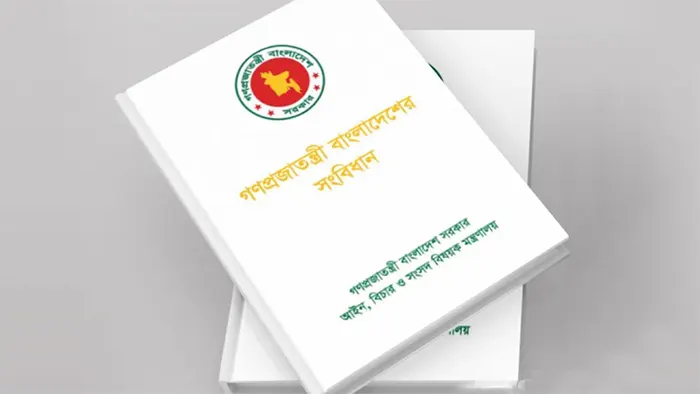
উৎস: ১৯৭১-এর সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম এবং ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার দুনিয়া কাঁপানো অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণআকাঙ্ক্ষাভিত্তিক সংবিধান প্রণয়নে ‘সংবিধান সংস্কার’ করা, ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ সংবিধানে জনগণের সার্বভৌমত্বকে সঙ্গতিপূর্ণ উপায়ে ও ন্যায় সঙ্গতভাবে বণ্টন করা হয়। ভোটাধিকার প্রধানত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক সাম্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রাথমিক শর্ত। এ কারণেই বলা হয়- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা হলো জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত, নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত শাসনব্যবস্থা।
জনগণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং সরকারের আইনগত সার্বভৌমত্ব, সুনির্দিষ্ট ও ভারসাম্যপূর্ণ না হওয়ায় ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং সংবিধান হবে স্থায়ী ও স্থিতিশীল। তাই বিদ্যমান সংবিধানকে বাতিল না করে সংস্কার বা সংশোধন অথবা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা সংযোজন করাই হবে মৌলিক কর্তব্য। সংবিধানকে সর্বোচ্চ আইন হিসেবে গ্রহণ করার পেছনে যে যুক্তি কাজ করে, সেটাই হলো সংবিধানের নৈতিক ভিত্তি। এটা সমস্ত জনগণের জন্য একটি দিক নির্দেশনা (এঁরফরহম ঝঃধৎ)। সংবিধানের প্রস্তাবনা হলো- রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের আত্মজীবনী বা সারসংক্ষেপ।
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার- এই ত্রয়ী আদর্শকে প্রজাতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তা ধারণ, লালন না করায় জাতীয় চেতনা এক ভয়াবহ ভিন্নপথে প্রভাবিত হয়েছে এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করেছে। অথচ এই ভাবাদর্শকে নিয়েই রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি প্রণয়ন করতে পারলে, মানুষের আকাঙ্ক্ষাসমূহ সার্থক ও চরিতার্থ লাভ করতে পারবে। ’৭২-এর সংবিধান, এই ভূখণ্ড ও জনগোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজনে নিজেরাই প্রণয়ন করে। যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান সংবিধানের মৌলিক বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করছি।
নতুন প্রস্তাবনা
আমরা জনগণ, দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে বিশেষ করে ’৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, অগ্নিঝরা মার্চের পতাকা উত্তোলন, স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ, ৭ই মার্চ-সহ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অতিক্রম করে ’৭১-এর সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি।
আমরা আরও অঙ্গীকার করছি, যেসকল মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের দার্শনিক ভিত্তিতে বীর শহীদগণ আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, সে ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণ হবে। সংবিধানই রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নকশা, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার রূপ-প্রকৃতি-চরিত্র নির্ধারিত হবে।
আমরা আরও অঙ্গীকার করছি যে
১) রাষ্ট্রের আদর্শ: ক) ‘সাম্য’, খ) ‘মানবিক মর্যাদা’ ও গ) ‘সামাজিক সুবিচার’ এই ত্রয়ী রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি, ঘ) ‘গণতন্ত্র’ হবে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং ঙ) নাগরিকের ‘জীবন সুরক্ষা’ হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এই পাঁচটি হবে রাষ্ট্রের দার্শনিক ও প্রায়োগিক ভিত্তি।
২) গণতন্ত্র: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হবে ‘গণতন্ত্র’ অর্থাৎ উবসড়পৎধপু রং ধ এড়াবৎহসবহঃ ড়ভ ঃযব চবড়ঢ়ষব নু ঃযব চবড়ঢ়ষব ধহফ ভড়ৎ ঃযব চবড়ঢ়ষব.
৩) জীবন (খরভব): রাষ্ট্র যেকোনো নাগরিক বা জনগণের ‘জীবন সুরক্ষার’ প্রশ্নটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে (ঐরমযবংঃ চৎরড়ৎরঃু ড়হ খরভব চৎড়ঃবপঃরড়হ)।
৪) সম্প্রীতি (ঐধৎসড়হু): সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণার্থে সকল ধর্ম-বর্ণের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব এবং সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষা করা হবে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।
৫) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (ঈড়সসরঃঃবফ): মানুষের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারে স্বৈরাচার বা ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্র কখনো ফিরে আসবে না, প্রজাতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রূপান্তর করে বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণ করাই হবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
৬) দৃঢ় প্রতিজ্ঞ (উবঃবৎসরহবফ): শুধুমাত্র জনগণের অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, কোনো বাইরের শক্তি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সংবিধানের দর্শন অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।
৭) জাতীয় ঐক্য (ঘধঃরড়হধষ পড়হংবহংঁং): স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলার মৌলিক নিশ্চয়তা হবে জাতীয় ঐক্য এবং সকল অপশক্তি মোকাবিলা করার প্রেরণা। জাতীয়তাবাদ এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নিশ্চিত করা।
৮) নির্দেশনা (এঁরফবফ): ‘সাম্য’, ‘মানবিক মর্যাদা’ ও ‘সামাজিক সুবিচার’- এই ত্রয়ী দর্শনের ভিত্তিতে দেশজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধারণ করে এবং ১৯৭১ ও ১৯২৪-এর নির্দেশনায় পরিচালিত হওয়া।
৯) আমাদের ঘোষণা (ডব উবপষধৎবফ): রাষ্ট্রের সকল আইনের উৎস হবে ‘মানবিক মর্যাদা’ (ঐঁসধহ ফরমহরঃু) সুরক্ষা করা। রাষ্ট্র সকল মানুষের পূর্ণ মানবিক মর্যাদা সুনিশ্চিত করবে। রাষ্ট্র কোনো অবস্থায় মানুষের মর্যাদা বিপন্ন করবে না।
আমরা আরও দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ স্বাধীন সত্তায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক-সহ সকল ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা লাভ এবং জাতীয় মুক্তিকে ত্বরান্বিত করে মানব জাতির অগ্রসরমান আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, শান্তিপূর্ণ বিশ্বের ঐতিহাসিক সম্ভাবনাকে বিবেচনায় নিয়ে বৈশ্বিক রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারি।
সমস্ত জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির মতাদর্শিক নির্দেশনা সম্বলিত মহৎ কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হবে প্রজাতন্ত্রের সংবিধান। এই সংবিধানকে কোনো দল বা গোষ্ঠী কর্তৃক ক্ষমতার হাতের খেলনা বা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে বল প্রয়োগের সুযোগ নিলে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই হবে জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার।
জাতির দীর্ঘ লড়াইয়ের মহান অর্জনগুলো বিশেষ করে ভাষা আন্দোলন, রক্তঝরা মার্চ-এর ঐতিহাসিক ঘটনাসহ ’৭১ ও ’২৪-এর গণহত্যার রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্যদিয়ে গড়ে ওঠা গণ-অভিপ্রায়ের প্রতিফলন হবে, বৈষম্যমুক্ত গণমুখী রাষ্ট্র বিনির্মাণের পূর্বশর্ত। সংবিধান হবে জাতীয় ঐতিহ্য ও গণআকাঙ্ক্ষার-অভিপ্রায়ের প্রতিচ্ছবি (গরৎৎড়ৎ ড়ভ হধঃরড়হধষ ধহফ ংড়পরধষ ধংঢ়রৎধঃরড়হ)।
প্রজাতন্ত্র বিনির্মাণের আইনগত ও দার্শনিক নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ১০ই এপ্রিলকে ‘প্রজাতন্ত্র দিবস’ হিসেবে চিহ্নিত করা।
এই সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করা সকল নাগরিকের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর এই জনগোষ্ঠীর পক্ষে প্রথম সংবিধান যে গণপরিষদ রচনা ও বিধিবদ্ধ করে সমবেতভাবে গ্রহণ করেছিল তার কাঠামোগত ও মৌলিক সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাবনা গৃহীত হলে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূরণে সহায়ক হবে। বিদ্যমান সংবিধানের যে সকল অনুচ্ছেদের বা দফা কিংবা উপদফার শুধুমাত্র সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:
প্রথম ভাগ
প্রজাতন্ত্র (প্রতিস্থাপিত)
১। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যা “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ” হিসেবে পরিচিত হবে।
রাষ্ট্রধর্ম (প্রতিস্থাপিত)
২। প্রজাতন্ত্র সকল ধর্মের অর্থাৎ ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান-সহ অন্যান্য ধর্ম পালনে সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার নিশ্চিত করবে।
রাষ্ট্রভাষা (প্রতিস্থাপিত)
৩। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। তবে অন্য জনগোষ্ঠীর ভাষা বিকাশেও রাষ্ট্র কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ করবে না।
জাতির পিতার প্রতিকৃতি (প্রতিস্থাপিত)
৪। আইন দ্বারা নির্ধারিত প্রতিষ্ঠাতা অভিভাবক (ঋড়ঁহফরহম ঋধঃযবৎং) ফাউন্ডিং ফাদার্সদের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহে সংরক্ষিত হবে।
নাগরিকত্ব (প্রতিস্থাপিত)
৬। (ক) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে।
(খ) বাংলাদেশের বাঙালি জনগোষ্ঠী জাতি হিসেবে বাঙালি। অন্যান্য জাতিসত্তার নাগরিকগণও নিজ নিজ জাতীয় পরিচয়ে পরিচিত হতে পারবে কিন্তু নাগরিক হিসেবে সকলেই বাংলাদেশি।
সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি (প্রতিস্থাপিত)
৭। (ক) কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ‘গণতন্ত্র’কে প্রতারণার মাধ্যমে সমগ্র জনগণের ভোটাধিকার এবং অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে আইনগত ও নৈতিকভাবে সংবিধানের মর্মবস্তুকে উপেক্ষা করে সংবিধানের প্রতি জনগণের আস্থা, বিশ্বাস এবং প্রত্যয় বিনষ্ট করলে আইনের আওতায় আনা হবে।
(খ) নির্বাচনকে প্রতারণা বা অপকৌশল করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ন বা বাতিল করলে জনগণের অভ্যুত্থান, বিদ্রোহ বা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকবে। যা জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।
সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য (প্রতিস্থাপিত)
৭(খ) ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন হবে। মৌলিক রূপান্তরে গণভোটের ব্যবস্থা থাকবে। তবে
১) জনগণ সকল সার্বভৌমত্বের মালিক।
২) সংবিধানের প্রাধান্য।
৩) গণতন্ত্র।
৪) প্রজাতান্ত্রিক সরকার।
৫) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা।
৬) রাষ্ট্রের তিন বিভাগের ক্ষমতার ভারসাম্য বিনষ্ট হতে পারে বা খর্ব করতে পারে, তা সংশোধন অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
দ্বিতীয় ভাগ
রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ (প্রতিস্থাপিত)
৮। রাষ্ট্র পরিচালনার দিক ও নির্দেশনামূলক নীতিসমূহ:
(১) ক) জাতীয়তাবাদ: বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন, বিনির্মাণ ও বিকাশের অপরিহার্য শর্ত এবং রাজনীতির অন্যতম নির্ণায়ক উপাদান জাতীয়তাবাদ। সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ এবং আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদ হবে মূল প্রেরণা। জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরেও ক্রিয়াশীল। জাতীয়তাবাদকে আরও বিকশিত করে বিশ্বের অন্যান্য জাতিসত্তার সমকক্ষ এবং জাতিত্বকে আরও উন্নত করতে হবে। ঐক্য-সংহতি এবং আত্মরক্ষার ভিত্তি হবে জাতীয়তাবাদ।
খ) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আত্মপরিচয়ের প্রশ্নেও রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা কোনো বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।
গ) ঔপনিবেশিকতার বিলোপসাধন করে সাম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের প্রতিটি জাতিসত্তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করাকে রাষ্ট্র অগ্রাধিকার প্রদান করবে।
২) বৈষম্যহীন সমাজ: আর্থ-সামাজিক, অসাম্য ও নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা
অতিক্রম করে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করাই হবে প্রজাতন্ত্রের মূল লক্ষ্য।
মানুষের ওপর মানুষের শোষণ হতে মুক্তি লাভ করার জন্য সামাজিক বিপ্লবের দ্বারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা রূপান্তর করাই হবে চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। রাষ্ট্র এমন কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারবে না, যা উপরোক্ত ত্রয়ী আদর্শকে খর্ব বা ক্ষুণ্ন করতে পারে।
৩) অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলভিত্তি হবে সমাজের সকল অংশের মানুষের অংশগ্রহণভিত্তিক অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র। গণতন্ত্রকে ক্রমাগত সম্প্রসারিত করতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণের স্তরে জনগণের সকল অংশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
৪) ধর্মীয় স্বাধীনতা বা সম্প্রীতি: রাষ্ট্র সকল ধর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। কারও কোনো ধর্মীয় অনুশাসনে রাষ্ট্র কোনোরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। সকল ধর্ম-বর্ণের সম্প্রীতি স্থাপন হবে সকল নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য।
৮(২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার দিকনির্দেশনা। আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র এই নির্দেশনাগুলো প্রয়োগ করবে। এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যা প্রদানে তা নির্দেশক হবে এবং রাষ্ট্র ও নাগরিকের কার্যের ভিত্তি হবে।
গণতন্ত্র ও মানবাধিকার (প্রতিস্থাপিত)
১১। প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে।
রাষ্ট্র পরিচালনার মূলভিত্তি গণতন্ত্র। সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রজাতন্ত্র। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার অবিচ্ছেদ্য। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবেও বাংলাদেশ হবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। সীমিত গণতন্ত্রকে ক্রমাগতভাবে অংশীদারিত্বের গণতন্ত্রে রূপান্তর করা, যেখানে সমাজের সকল অংশের-মানুষের মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে।
ক) প্রশাসনের সকল পর্যায়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল স্তরে সর্বস্তরের জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা (প্রতিস্থাপিত)
১২) ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতি বাস্তবায়নে:
ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার করা যাবে না।
খ) যেকোনো ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ বা বৈষম্য বিলোপ করা হবে।
আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন
(সংযোজিত)
২৫ (২) জাতীয় প্রতিরক্ষানীতি:
বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ঝুঁকিকে বিবেচনায় নিয়ে প্রতিরক্ষা প্রশ্নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।
১) রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার স্বার্থে আক্রমণাত্মক নয়, প্রতিরোধমূলক নীতির ভিত্তিতে অবিলম্বে ‘জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিল’ গঠনপূর্বক যুগোপযোগী জাতীয় প্রতিরক্ষানীতি প্রণয়ন করা।
২) ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে সকল নারী-পুরুষকে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণসহ আইন প্রণয়ন করা।
তৃতীয় ভাগ
মৌলিক অধিকার
২৮। ধর্ম, গোষ্ঠী প্রভৃতি কারণে বৈষম্য (প্রতিস্থাপিত)
১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ, তৃতীয় লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।
২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে সকল লিঙ্গ সমান অধিকার লাভ করবে।
৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ, তৃতীয় লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশ কিংবা কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কাউকেই কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।
(৪) নারী, তৃতীয় লিঙ্গ বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোনো সরকারি নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা (প্রতিস্থাপিত)
২৯। ১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।
২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।
৩) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই
(ক) নাগরিকদের যেকোনো অনগ্রসর অংশ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হতে,
(খ) কোনো ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যেকোনো আইন কার্যকর করা হতে,
(গ) যে শ্রেণির কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যেকোনো শ্রেণির নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।
বিদেশি খেতাব, প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ
৩০। রাষ্ট্র শ্রেণিবৈষম্য বা সামাজিক বৈষম্যের বীজ বপন করতে পারে এমন কোনো খেতাব প্রদান করবে না। তবে, গৌরবজনক বা বিভিন্ন বিষয়ে উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে সম্মানসূচক পুরস্কার বা অ্যাওয়ার্ড দিতে পারবে।
ক) রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো নাগরিক কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট হতে কোনো রকম খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করবে না।
চলাফেরার স্বাধীনতা (প্রতিস্থাপিত)
৩৬। বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, যেকোনো স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।
তবে, অবাধ অধিকারের নামে বৈষম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থায় দুর্বল শ্রেণি বা ক্ষুদ্র-জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্র ন্যায়সঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।
সমাবেশের স্বাধীনতা (প্রতিস্থাপিত)
৩৭। শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হওয়ার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।
ক) গোলযোগ বা সংঘাত-সংঘর্ষ অথবা রক্তপাতের আশঙ্কা থাকলে আদালতের নির্দেশে অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকায় সাময়িক বাধা-নিষেধ আরোপ করতে পারে।
চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা (প্রতিস্থাপিত)
৩৯। ১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হলো।
২) রাষ্ট্রে নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত বা নৈতিকতার স্বার্থে ব্যক্তি এবং সমাজের অধিকারের সমন্বয়পূর্বক ন্যায়সঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে।
গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ (প্রতিস্থাপিত)
৪৩। ক) প্রত্যেক নাগরিকের প্রবেশ, তল্লাশি ও আটক হতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার থাকবে; এবং
খ) ব্যক্তিগত ফোন, কম্পিউটার চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকবে।
গ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জন-শৃঙ্খলার স্বার্থে আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে উপরোক্ত অনুচ্ছেদের (ক এবং খ) প্রতিশ্রুত অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না।
শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন
প্রতিস্থাপন
৪৫। কোনো শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোনো শৃঙ্খলামূলক আইনের যেকোনো বিধান উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্য পালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষা নিশ্চিত করবে। তবে অন্যায্য বরখাস্ত, জোরপূর্বক পদত্যাগ, অবসর, অসামঞ্জস্যপূর্ণ শাস্তি এবং অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ওপর বেআইনি নিষেধাজ্ঞা আরোপে আইনগত অধিকার প্রযোজ্য হবে।
নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য (সংযোজিত)
মৌলিক কর্তব্য
৪৭। (খ)
১. প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন এবং সর্বশক্তি দিয়ে মাতৃভূমিকে রক্ষা, বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান করা।
২. সেই সব মহৎ আদর্শ লালন করা যা সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম, আন্দোলন-লড়াই ও গণঅভ্যুত্থানে আত্মোৎসর্গ করার অনুপ্রেরণা জুুগিয়ে ছিল।
৩. দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার প্রশ্নটি দল-মত-পথের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া।
৪. ধর্ম-বর্ণ আঞ্চলিকতা-সহ সকল ধরনের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সকলের মাঝে সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশীদারিত্বমূলক সমাজ গঠন করা।
৫. দেশজ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, স্থাপত্য, মূল্যবোধ, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা।
৬. নদী, জলাশয়, বন, বৃক্ষ-সহ প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা এবং অন্যান্য প্রাণীদের প্রতি সংবেদনশীল ও সহানুভূতিশীল হওয়া।
৭. নারীর প্রতি অসম্মানজনক, অবমাননাকর ও অমর্যাদাকর মানসিকতা পরিহার করা।
৮. একটি জ্ঞাননির্ভর নৈতিক-সমাজ গঠনে জনগণের জানমাল রক্ষা-সহ যেকোনো ধরনের সহিংসতাকে পরিহার করা।
৯. বৈষম্যমুক্ত ন্যায্য সমাজের পূর্বশর্ত হবে প্রত্যেক নাগরিকের ন্যায্যতা উপলব্ধির বোধ ও শুভ চিন্তার সামর্থ্য অর্জন করা।
১০. আত্ম-বিকাশের উৎকর্ষতার লক্ষ্যে ব্যক্তি এবং সমষ্টিগতভাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং মহৎ কীর্তি দ্বারা জীবনকে ক্রমাগত মহিমান্বিত করা।
চতুর্থ ভাগ
নির্বাহী বিভাগ
১ম পরিচ্ছেদ রাষ্ট্রপতি (সংযোজিত)
৪৮। (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ (সংসদের উভয় কক্ষ) কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।
(২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করবেন। এই সংবিধান ও অন্য কোনো আইনের দ্বারা তাকে প্রদত্ত এবং তার ওপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।
(৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে প্রধানমন্ত্রী, ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি এবং বিচারক নিয়োগ ছাড়াও নির্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন-সহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্টপতি তার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করবেন; তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোনো পরামর্শ দান করেছেন কি না এবং করে থাকলে কী পরামর্শ দান করেছেন, কোনো আদালত সেই সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের তদন্ত করতে পারবেন না।
(৪) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করলে যেকোনো বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করবেন।
৫) বাংলাদেশে একজন উপরাষ্ট্রপতি থাকবেন। যিনি সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন এবং পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের স্পিকার বা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করবেন।
৬) রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি হওয়ার যোগ্যতা:
কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হবেন না, যদি তিনি
(ক) ৩৫ বৎসরের কম বয়স্ক হন অথবা
(খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য না হন; অথবা
(গ) কখনো এই সংবিধানের অধীন অপসারিত হয়ে থাকেন।
ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার (প্রতিস্থাপিত)
৪৯। কোনো আদালত ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করার এবং যেকোনো দণ্ড মওকুফ বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে।
তবে শর্ত থাকে যে, তা অবশ্যই বিচক্ষণতা ও নৈতিকতার ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত হতে হবে।
রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ (প্রতিস্থাপিত)
৫০। ১) সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি চার বছর মেয়াদে তার পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।
২) একাধিক ক্রমে হোক বা না হোক দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতি পদে কোনো ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।
৩) রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতির নিকট এবং উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির নিকট স্বীয় পদ, ত্যাগ করতে পারবেন।
৪) রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্য হবেন না; সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর কেউ যদি রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হন, তাহলে রাষ্ট্রপতি হিসেবে কার্যভার গ্রহণের দিন থেকে তার সংসদ সদস্য পদ শূন্য হবে।
রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি (প্রতিস্থাপিত)
রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি
৫১। (১) এই সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদের হানি না ঘটিয়ে বিধান করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোনো কার্য করে থাকলে বা না করে থাকলে সেজন্য তাকে কোনো আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না, তবে এই দফা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণে কোনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন্ন করবে না।
(২) রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি কার্যভারকালে তার বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো প্রকার ফৌজদারি কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাবে না এবং
তার গ্রেপ্তার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত হতে পরোয়ানা জারি করা যাবে না।
রাষ্ট্রপতির অভিশংসন (প্রতিস্থাপিত)
রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির অভিশংসন
৫২। (১) এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাবে। এর জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হবে; স্পিকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হতে ১৪ দিনের পূর্বে বা ৩০ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হতে পারবে না এবং সংসদ অধিবেশন চলমান না থাকলে স্পিকার অবিলম্বে সংসদ আহ্বান করবেন।
(২) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত বা আখ্যায়িত কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট সংসদ, রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করতে পারবেন।
(৩) অভিযোগ-বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকবে।
(৪) অভিযোগ-বিবেচনার পর মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ হিসেবে ঘোষণা করে সংসদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে, প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার তারিখে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।
অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ (প্রতিস্থাপিত)
অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির অপসারণ
৫৩। (১) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতিকে তার পদ থেকে অপসারিত করা যাবে, এর জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে কথিত অসামর্থ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হবে।
(২) সংসদ অধিবেশনরত না থাকলে নোটিশ প্রাপ্তিমাত্র স্পিকার সংসদের অধিবেশন আহবান করবেন এবং একটি চিকিৎসা-পর্ষদ (অতঃপর এই অনুচ্ছেদে “পর্ষদ” বলে অভিহিত) গঠনের প্রস্তাব আহ্বান করবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হওয়ার পর স্পিকার তৎক্ষণাৎ উক্ত নোটিশের একটি প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন এবং তার সঙ্গে এই মর্মে স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করবেন যে, অনুরূপ অনুরোধ জ্ঞাপনের তারিখ হতে ১০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি যেন পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হওয়ার জন্য উপস্থিত হন।
(৩) অপসারণের জন্য প্রস্তাবের নোটিশ স্পিকারের নিকট প্রদানের পর হতে ১৪ দিনের পূর্বে বা ৩০ দিনের পর প্রস্তাবটি ভোটে দেয়া যাবে না এবং অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য পুনরায় সংসদ আহ্বানের প্রয়োজন হলে স্পিকার সংসদ আহ্বান করবেন।
(৪) প্রস্তাবটি বিবেচিত হওয়ারকালে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকবে।
(৫) প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি পর্ষদের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার জন্য উপস্থিত না হয়ে থাকলে ভোটে দেয়া যেতে পারে এবং সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।
অনুপস্থিতি প্রভৃতির-কালে রাষ্ট্রপতি (প্রতিস্থাপিত)
৫৪। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে ক্ষেত্রমতো রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।
২য় পরিচ্ছেদ
প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা (প্রতিস্থাপিত)
৫৫। (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করবেন, সেরূপ উপপ্রধানমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রী নিয়ে এই মন্ত্রিসভা গঠিত হবে।
(২) প্রধানমন্ত্রী সরকারের নির্বাহী প্রধান।
(৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে এবং এককভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন।
(৪) সরকারের সকল নির্বাহীব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হবে।
(৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কীরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হবে, রাষ্ট্রপতি তা বিধিসমূহ-দ্বারা নির্ধারণ করবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোনো আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয়নি বলে তার বৈধতা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।
(৬) রাষ্ট্রপতি সরকারি কার্যাবলী বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করবেন।
প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ
৫৭। একাধিক ক্রমে হোক বা না হোক দুই মেয়াদের অধিক প্রধানমন্ত্রী পদে কোনো ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।
৩য় পরিচ্ছেদ
স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা (প্রতিস্থাপিত)
৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকর স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় রূপান্তর করাসহ স্থানীয় প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, করারোপ করার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করবেন।
৪র্থ পরিচ্ছেদ
প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ সর্বাধিনায়কতা (প্রতিস্থাপিত/ সংযোজিত)
৬১। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত হবে এবং আইনের দ্বারা তার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হবে।
ক) সংসদের আইনের দ্বারা ‘জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিল’ গঠন করবে।
যুদ্ধ (প্রতিস্থাপিত)
৬৩। (১) উভয় সংসদের (উচ্চকক্ষ এবং জাতীয় সংসদ) সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না।
৫ম পরিচ্ছেদ
অ্যাটর্নি-জেনারেল (প্রতিস্থাপিত)
৬৪। (১) সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগ দান করবেন।
(২) অ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।
(৩) অ্যাটর্নি-জেনারেলের দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তার বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকবে।
(৪) রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করবেন।
পঞ্চম ভাগ
আইনসভা
১ম পরিচ্ছেদ
সংসদ-প্রতিষ্ঠা (প্রতিস্থাপিত)
৬৫। উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের সমন্বয়ে দেশের জাতীয় সংসদ (পার্লামেন্ট) হবে দুইকক্ষ বিশিষ্ট।
ক) ‘নিম্নকক্ষ’ হবে ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট। নিম্নকক্ষে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত এলাকাভিত্তিক নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবেন।
খ) ‘উচ্চকক্ষ’ ২০০ সদস্য বিশিষ্ট। উচ্চকক্ষে থাকবেন:-
১. শ্রম-কর্ম-পেশায় নিয়োজিত (শ্রমজীবী, কর্মজীবী, পেশাজীবী) ব্যক্তিদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য।
২. প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত নারী সদস্য।
৩. ‘ক্ষুদ্র জাতিসত্তা’র নাগরিকদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য।
৪. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য। (মূলত প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং আমলা-কর্মকর্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ অন্যান্য পেশার মধ্য থেকে)
৫. জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোট অনুযায়ী আনুপাতিক হারে রাজনৈতিক দলসমূহের মনোনীত সদস্য।
ক) ‘উচ্চকক্ষ’র অধ্যক্ষ থাকবেন উপরাষ্ট্রপতি।
খ) জাতীয় সংসদের (উভয় ‘কক্ষ’) মেয়াদকাল হবে ৪ (চার) বছর।
রাজনৈতিক দল থেকে পদত্যাগ (প্রতিস্থাপিত)
৭০। কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি (ক) সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবের উপর দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহলে সংসদে তার আসন শূন্য হবে।
ষষ্ঠ ভাগ
বিচারবিভাগ
১ম পরিচ্ছেদ
সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা (প্রতিস্থাপিত ও সংযোজিত)
৯৪। (১) “বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট” নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকবে এবং আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে তা গঠিত হবে।
(২) প্রধান বিচারপতি (যিনি “বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি” নামে অভিহিত হবেন) এবং প্রত্যেক বিভাগে আসন গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করবেন, সেরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে।
(৩) প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন। আপিল এবং হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকগণ ‘বিচারক’ হিসেবে অভিহিত হবেন।
(৪) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন।
(৫) বেঞ্চ গঠন এবং ভেঙে দেয়ার ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির ক্ষমতা, আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।
(৬) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ৭ সদস্যবিশিষ্ট ‘সাংবিধানিক আদালত’ থাকবে।
অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা (প্রতিস্থাপিত)
৯৯। (১) কোনো ব্যক্তি বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন করে থাকলে উক্ত পদ হতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হওয়ার পর তিনি কোনো আদালত বা কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করবেন না এবং প্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না।
অধস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা (প্রতিস্থাপন)
১১৬। বিচার-কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার-বিভাগীয় দায়িত্ব পালনরতদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) ও শৃঙ্খলা-বিধান সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত থাকবে।
সপ্তম ভাগ
নির্বাচন-অনুষ্ঠানের সময় (প্রতিস্থাপিত)
১২৩। (১) রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হলে মেয়াদ-সমাপ্তির তারিখের পূর্ববর্তী ৬০ দিন হতে ৯০ দিনের মধ্যে শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, যে সংসদের দ্বারা তিনি নির্বাচিত হয়েছেন সে সংসদের মেয়াদকালে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হলে সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ শূন্য পদ পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না এবং অনুরূপ সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের দিন হতে ৩০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শূন্য পদ পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
(২) মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে পদটি শূন্য হওয়ার পর ৯০ দিনের মধ্যে, তা পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
(৩) সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
ক) সংসদ ভেঙে যাওয়ার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে।
(৪) সংসদ ভেঙে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদের কোনো সদস্যপদ শূন্য হলে পদটি শূন্য হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে উক্ত শূন্যপদ পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, যদি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে, কোনো দৈব-দুর্বিপাকের কারণে এই দফার নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয়, তাহলে উক্ত মেয়াদের শেষ দিনের পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
একাদশ ভাগ
বিবিধ পদের শপথ (প্রতিস্থাপিত)
১৪৮। তৃতীয় তফসিল
১) রাষ্ট্রপতির শপথবাক্য পাঠ পরিচালনা করবেন প্রধান বিচারপতি। স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার অনুরূপ শপথ পাঠ করবেন প্রধান বিচারপতির নিকট।
২ (ক) ১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন সংসদ ভাঙার পর অনুষ্ঠিত সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হওয়ার পর স্পিকার কর্তৃক নির্ধারিত দিনে বা একাধিক দিনে সংসদ সদস্যগণ শপথ পাঠ করবেন।
শপথ ভঙ্গের দায় (সংযোজন)
১৪৮ (ক) যারা তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা লংঘন বা ভঙ্গ করবেন তাদের আইন মোতাবেক দায় নির্ধারিত হবে।
(ব্যাখ্যা)
১৫২ (১)-এ প্রদত্ত সকল ব্যাখ্যার মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রতিস্থাপিত হবে: “রাষ্ট্র” বলতে জনগণ, ভূমি, সরকার, সার্বভৌমত্ব, সংসদ ও সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত।
“শৃঙ্খলা-বাহিনী” অর্থ:
(ক) স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনী।
(খ) আইনের দ্বারা এই সংজ্ঞার অর্থের অন্তর্গত বলে ঘোষিত যেকোনো শৃঙ্খলা-বাহিনী।
সংবিধান প্রবর্তন (প্রতিস্থাপিত)
১৫৩ (১) এই সংবিধানকে ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান’ বলে উল্লেখ করা হবে। যা ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে ‘সংবিধান প্রবর্তন’ বলে অভিহিত করা হলেও তাতে সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের অভিপ্রায় পূরণের উপযোগী চেতনা প্রতিফলিত হয়নি বরং সংবিধানকে শাসকদলের হাতের খেলনায় পরিণত করেছে। পরবর্তীকালে আন্দোলন-লড়াই ও ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে সংবিধান সংস্কারের প্রশ্নটি ঐতিহাসিক কর্তব্য বলে বিবেচিত হওয়ায় এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই সংবিধানের আমূল সংস্কার করা হলো।